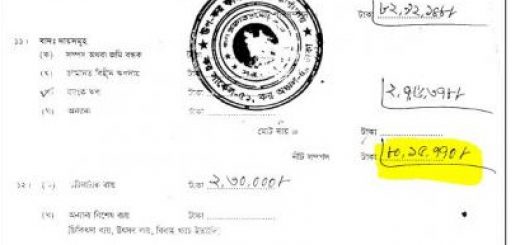বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ আসে সম্ভবত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী ছিলেন মন্ত্রণালয়েরই একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তারপর পাটমন্ত্রী, তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী, নৌপরিবহনমন্ত্রী, জ্বালানি উপদেষ্টা, শিল্পমন্ত্রী, সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী, সাবেক রেলমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ বা বিচ্যুতির মাধ্যমে দুর্নীতিবান্ধব একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়।
এমন পরিস্থিতির কিছু উদাহরণ দিই। প্রথমত, সরকারপ্রধান নির্বাচন চলাকালীন মন্ত্রী ও সাংসদদের সম্পত্তির বার্ষিক বিবরণী দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও এ থেকে তাঁরা বিরত থাকেন। দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজারে লুটপাটের ঘটনায় একজন মন্ত্রীর পরিবার ও সরকারি দলের কয়েকজন নেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে আসার পরও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বিরত থাকে। তৃতীয়ত, বিনা টেন্ডারে বহুল বিতর্কিত কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সরকারের কাছের লোকজনকে প্রদান করার সন্দেহজনক কার্যক্রমকে তদন্তের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য আগেই দায়মুক্তি আইন পাস করা হয়। চতুর্থত, প্রকিউরমেন্ট রুল সংশোধন করে বিনা অভিজ্ঞতা ও বিনা দক্ষতায় দুই কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করে সরকার তার লোকজনকে অবাধে কাজ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পঞ্চমত, টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট, ২০১০-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মন্ত্রণালয়কে দিয়ে দেওয়া হয়। এর পরপরই দেশে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার হিড়িক পড়ার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে, এর সঙ্গে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। ষষ্ঠত, প্রতিবছর বাজেটে কালোটাকা সাদা করা এবং অবাধে বিনিয়োগ করার সুযোগ দিয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ আড়াল করার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
রাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে, সেখানেও চলে নানা হস্তক্ষেপ। যেমন, উচ্চ আদালতে নিয়োগ এবং নিম্ন আদালতে পোস্টিংয়ে দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। সংসদের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কমিটির (যেমন, পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি বা অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) দায়িত্ব দেওয়া হয় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের।
প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমনে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান দুদকের শক্তিও খর্ব করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কমিশনের স্বাধীনতা ও তদন্তকালীন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং এর এখতিয়ার বাড়িয়ে (যেমন, মানি-লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে অপরাধ তদন্ত করার ক্ষমতা) দুটো সংশোধনী অর্ডিন্যান্স আকারে গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সেগুলো নাকচ করে দেয়। এমনকি সরকার এমন কিছু সংশোধনীর উদ্যোগ নেয়, যা কার্যকর হলে দুদকের দুর্নীতি দমন অভিযান ম্রিয়মাণ হতে বাধ্য। যেমন, সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হয় যে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তদন্তের জন্য কমিশনকে সরকারের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত সংশোধনীতে কমিশনের চেয়ারম্যানের কিছু ক্ষমতা সরকার কর্তৃক নিয়োগ পাওয়া সচিবকে অর্পণ, রাষ্ট্রপতির (আসলে প্রধানমন্ত্রী) কাছে কমিশনের জবাবদিহি ও দুর্নীতির মামলা মিথ্যা হলে উল্টো অভিযোগকারীকে কারাদণ্ডের বিধানের কথা বলা হয়। নাগরিক সমাজের চাপের মুখে পূর্বানুমোদনের বিধানটি প্রত্যাহার করা হলেও বাকি আপত্তিকর বিষয়গুলোতে সরকারের অবস্থান এখনো পরিষ্কার নয়।
দুদককে হেয় ও দর্শনগতভাবে দুর্বল করার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি নেওয়া হয় ঢালাওভাবে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সব দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করে। এর মধ্যে কিছু হয়রানিমূলক মামলা হয়তো ছিল, কিন্তু কিছু মামলা, বিশেষ করে জ্ঞাত উৎসবহির্ভূত সম্পত্তিসংক্রান্ত মামলাগুলো ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। সরকার তার লোকদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়কের আমলে দায়ের করা এসব মামলা নির্বিচারে প্রত্যাহার করলেও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে সব মামলা জারি রাখে। আর এর মাধ্যমেই সম্ভবত দুদককে কীভাবে কাজ করতে হবে, তার একটি অলিখিত নির্দেশনা সরকার দিয়ে দেয়। দুদক সেই নির্দেশনা ভালোভাবেই পড়তে পেরেছে মনে হয়। গত তিন বছরে কোনো মন্ত্রী বা এই সরকারের আমলের প্রভাবশালী আমলা ও বড় ব্যবসায়ীর দুর্নীতির কোনো হদিস তারা পায়নি; বরং সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বা আবুল হোসেনের মতো মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বা সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকার পরও দুদককে দেখা গেছে এদের নির্দোষ হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে।